বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২ মাঘ ১৪৩২
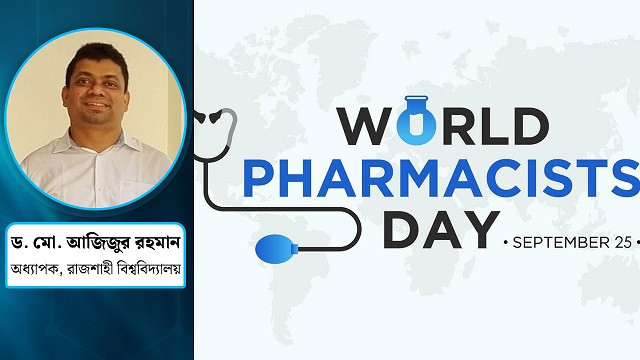
ছবি : সংগৃহীত
২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস। ফার্মাসিস্টদের সর্ববৃহৎ সংগঠন আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশন (International Pharmaceutical Federation বা FIP) এর উদ্যোগে ২০০৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ফার্মাসিস্টরা এ দিবসটি খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করে আসছে।
২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ হলো ১৯১২ সালের এ দিনে নেদারল্যান্ডস-এ আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবায় ফার্মাসিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে জনগণের নিকট তুলে ধরা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে ফার্মাসিস্টদের বিভিন্ন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করায় এ দিবস পালন করার উদ্দেশ্য।
আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশন প্রতিবছর বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবসের একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো—‘Think Health, Think Pharmacist’ অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করুন, ফার্মাসিস্টের কথা মনে রাখুন।
‘ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩’ অনুযায়ী- “একজন ফার্মাসিস্ট হলেন বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল কর্তৃক ‘এ’ ক্যাটাগরিতে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি”। বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে নিবন্ধিত হতে একজন ফার্মাসিস্টকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের বিফার্ম (অনার্স) বা পাঁচ বছরের বিফার্ম (প্রফেশনাল) ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩ অনুযায়ী ‘ফার্মাসিস্ট’ হলেন ফার্মেসিতে ডিগ্রিধারী একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট।
আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী—“ফার্মাসিস্টরা হলেন ওষুধ প্রস্তুত ও ওষুধের উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। রোগীরা যাতে ওষুধ থেকে সর্বোচ্চ চিকিৎসাগত উপকার পান, ফার্মাসিস্টরা তা নিশ্চিত করেন। ফার্মাসিস্টরা ওষুধ ও তার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সর্বাধিক বিশদ জ্ঞানসম্পন্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, যারা নিরাপদ, কার্যকর ও যৌক্তিক ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখেন।”
বিশ্বে ও বাংলাদেশে ফার্মাসিস্টের সংখ্যা কত, তারা কোথায় কর্মরত?
আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে বর্তমানে ফার্মাসিস্টের সংখ্যা ৫৫ লাখ ৭০ হাজার। এ বিশাল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রিধারী ফার্মাসিস্টদের প্রায় ৫৮ শতাংশ কাজ করেন কমিউনিটি ফার্মাসিস্ট হিসেবে, ৩২ শতাংশ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে, বাকি ১০ শতাংশ কাজ করেন ওষুধ কোম্পানির বিভিন্ন সেক্টরে (যেমন- ওষুধ প্রস্তুত, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি), বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে, ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইত্যাদি।
তবে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় ফার্মাসিস্টদের গড়ে প্রায় ৫৫ শতাংশ ওষুধ কোম্পানির বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল এ পর্যন্ত ২৩ হাজার ৮৫০ জন গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেছে, যারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থেকে ফার্মেসিতে স্নাতক ডিগ্রিধারী।
আমাদের সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফল বলছে আমাদের দেশের ফার্মাসিস্টদের প্রায় ৮০ শতাংশ ওষুধ কোম্পানির বিভিন্ন শাখা যেমন- উৎপাদন (২৫.৪৪ শতাংশ), গবেষণা ও উন্নয়ন (১৪.২ শতাংশ), কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (১৩.৬১ শতাংশ), পণ্য ব্যবস্থাপনা (১০.৬৭ শতাংশ) ও মান নিয়ন্ত্রণ (৭.৬৯ শতাংশ) শাখায় কাজ করেন।
দেশের মাত্র ১-২ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট কাজ করেন কমিউনিটি ও হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে। অথচ বহির্বিশ্বে এ দুটি সেক্টরেই কাজ করেন প্রায় ৮০-৯০ ভাগ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট।
ফার্মাসিস্টদের কাজ কী?
স্বাস্থ্যসেবায় যে কয়টি পেশা জড়িত তার মধ্যে অন্যতম হলো চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট ও নার্স। স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসক ও নার্সের ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণের নিকট বেশ স্পষ্ট হলেও, ফার্মাসিস্টের ভূমিকা ততটা পরিষ্কার নয়। কারণ, দেশে সরাসরি রোগীদের সেবায় ফার্মাসিস্টদের কাজ করার সুযোগ এখনো তৈরি হয়নি। উন্নত বিশ্বে চিত্রটা অন্যরকম।
বিশ্বের মোট গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টের প্রায় ৬০ শতাংশ কমিউনিটি ফার্মাসিস্ট। অর্থাৎ চার-পাঁচ বছরের বিফার্ম/এমফার্ম ডিগ্রি অথবা চার থেকে ছয় বছরের ডক্টর অব ফার্মেসি (ফার্মডি) ডিগ্রি অর্জনের পর ফার্মাসিস্টদের একটি বড় অংশ কমিউনিটি ফার্মাসিস্ট হিসেবে উচ্চ বেতন ও সম্মানের সাথে ফার্মেসিতে কাজ করেন। এসব কমিউনিটি ফার্মাসিস্টরা অনেকে চাকুরীজীবী আবার অনেকে নিজের প্রতিষ্ঠান নিজেই পরিচালনা করেন।
প্রশ্ন হলো, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা আছে এমন দেশে ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্টরা এমন কী কাজ করেন যে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিফার্ম/এমফার্ম/ফার্মডি ডিগ্রি অর্জন করতে হয় এবং খুব কঠিন রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষায় পাস করে ফার্মাসিস্ট হিসেবে প্র্যাকটিস করার জন্য লাইসেন্স পেতে হয়?
একজন কমিউনিটি ফার্মাসিস্টর মূল কাজ হলো প্রেসক্রিপশন যাচাই ও মূল্যায়ন করা, প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে সঠিক ওষুধ সরবরাহ করা এবং ওষুধে গ্রহণ ও সংরক্ষণের নিয়ম ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে পরামর্শ প্রদান করা।
তাছাড়া ফার্মাসিস্টরা রোগীদের ফার্মাসিউটিক্যাল সেবাও প্রদান করেন যার আওতায় ড্রাগ-ড্রাগ ইন্টার্যাকশন চিহ্নিতকরণ, ওষুধ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ, সঠিক ওষুধ সঠিক ডোজে প্রদান নিশ্চিতকরণ, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা রোগীদের বিশেষ সেবা প্রদান ইত্যাদি।
বিশ্বে ফার্মাসিস্টদের ২য় প্রধান কর্মক্ষেত্র হলো হাসপাতাল ও ক্লিনিক। বিশ্বের মোট ফার্মাসিস্টদের প্রায় ৩২ শতাংশ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সরাসরি রোগীর সেবায় কাজ করে থাকেন।
হসপিটাল ও ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টের মূল কাজ হলো রোগীর প্রেসক্রিপশন যাচাই করা ও ওষুধ বিতরণ করা, প্রেসক্রিপশনে ওষুধের সঠিক ডোজ, রুট ও সময় ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করা ও ভুল থাকলে সংশোধন করা, চিকিৎসক ও নার্সকে ওষুধের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া, জটিল রোগীর (ক্যান্সার, কিডনি) জন্য বিশেষ ওষুধ ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি।
ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত ফার্মাসিস্টরা ওষুধ প্রস্তুত, গবেষণা, মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ, ফর্মুলেশন ইত্যাদি শাখায় কাজ করেন। আমাদের দেশে বেশিরভাগ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট এসব কাজে জড়িত। সরাসরি রোগীর সেবায় তাদের ভূমিকা নাই বললেই চলে, যা উন্নত স্বাস্থ্যসেবার প্রধান বাধা।
দেশে ফার্মেসিতে, হাসপাতালে ও ক্লিনিকে ফার্মাসিস্ট নেই বললেই চলে, কিন্তু জনগণ ফার্মাসিস্টের প্রয়োজন অনুভব করছে কি?
এ নিয়ে এখনো কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবে রোগীরা প্রতিনিয়ত ওষুধ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন যেগুলো সমাধান করতে পারেন ফার্মাসিস্টরা।
ফার্মাসিস্টদের কাজ নিয়ে সাধারণ জনগণের ধারণা নেই বললেই চলে, ফার্মাসিস্টের ইন্টারভেনশন কেন জরুরি তা জনগণ উপলব্ধি করতে পারেন না। একটি আদর্শ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ফার্মাসিস্টের নিরীক্ষণ ছাড়া কোনো প্রেসক্রিপশনের ওষুধ সরবরাহ অকল্পনীয়।
প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসক অনেক সময় ওষুধের ভুল ডোজ লিখে ফেলেন কারণ একজন চিকিৎসকের হাজার হাজার ওষুধের ডোজ মনে রাখা সহজ কথা নয়। অধিকন্তু, রোগীর রোগের ধরণ ও তীব্রতা, বয়স, ওজন, কিডনি ও লিভারের সক্ষমতা, কো-মর্বিডিটি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে একই ওষুধ একেক রোগীকে একেক ডোজে প্রদান করতে হয়।
চিকিৎসকদের প্রচুর কর্মব্যস্ততার কারণে এত ওষুধের নাম ও ডোজ মনে রাখা বেশ জটিল। আমাদের দেশে সামাজিক কারণে চিকিৎসকরা রেফারেন্স বই দেখে ডোজ নির্ধারণ করবেন তা চাইলেও পারেন না, চাইলেও সময় পান না। তাই, প্রেসক্রিপশনে ওষুধের ডোজে ভুল হওয়া খুব সাধারণ একটি ঘটনা।
সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বেই ভুল ডোজের প্রেসক্রিপশনের হার গড়ে ৩০-৪০ শতাংশ। উন্নত বিশ্বেও ওষুধের ভুল প্রেসক্রিপশন খুব কমন, যেগুলো সংশোধনে ফার্মাসিস্টরা কাজ করে থাকেন। সৌদি আরবের রিয়াদের একটি বড় হাসপাতালে ২০১৭ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক (৫৪.৩ শতাংশ) প্রেসক্রিপশনে ভুল ডোজ প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল যেগুলো হসপিটাল ফার্মাসিস্টরা সংশোধন করে দেন।
এছাড়া যেসব দেশে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ প্রেসক্রিপশন করা হয় সেসব দেশে অনেক সময় চিকিৎসকরা ভুলক্রমে একই জেনেরিকের (ওষুধের মূল উপাদানের নাম) দুটি ওষুধ লিখে ফেলেন। কারণ, কোন কোন জেনেরিকের প্রায় শতাধিক ব্র্যান্ড আছে, যেগুলোর সব নাম একজন চিকিৎসকের জন্য মনে রাখা বেশ কঠিন।
উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে শুধু অ্যাজিথ্রোমাইসিনের প্রায় শতাধিক ব্র্যান্ড আছে। এর ফলে কোনো একজন চিকিৎসক একটি অপরিচিত বা নতুন ব্র্যান্ডের নাম প্রেসক্রিপশনে লিখলে তা আরেকজন চিকিৎসকের চেনা কঠিন হয়ে যায়। ফলে, কিছু পরিস্থিতিতে একই জেনেরিকের দুটি ভিন্ন ব্র্যান্ড অনেকসময় ভুল করে লিখে ফেলেন, যা রোগীর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।
যেসব রোগী একাধিক রোগ যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যালার্জি ইত্যাদিতে ভুগছেন তাদের অনেকগুলো ওষুধ খেতে হয় এবং একেকটি একেক সময়ে খেতে হয়। এসব রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধের সঠিক ডোজ নির্ণয় করা ও রোগী সঠিক সময়ে সেগুলো খেতে পারবে কিনা তা নিশ্চিত করা বেশ জটিল। সময়ের অভাবে চিকিৎসকরা অনেকসময় ড্রাগ-ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন এড়িয়ে যান, যা রোগীর জন্য ভয়াবহ বিপজ্জনক হতে পারে।
অনেক সময়, চিকিৎসকরা রোগীর অন্য রোগের উপস্থিতি বা রোগী অন্য কোন ওষুধ খাচ্ছেন কিনা তার ইতিহাস পুরোপুরি যাচাই করার সময় পান না। কিছু ওষুধ আছে যেগুলো রোগীর অন্য রোগকে বাড়িয়ে দিয়ে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, যেসব রোগী মায়াস্থেনিয়া গ্রাভিস (Myasthenia Gravis) (এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অটোইমিউন ডিজর্ডার) রোগে ভুগছেন তাদের জন্য কিছু ওষুধ যেমন সিপ্রোফ্লক্সাসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন, বিটা-ব্লকার (অ্যাটেনোলল, প্রোপ্রানোলল ইত্যাদি) একদম নিষিদ্ধ। এসব ওষুধ মায়াস্থেনিয়া গ্রাভিস রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।
আমাদের দেশে রোগীদের ডেটাবেজ না থাকায় অনেকসময় রোগীদের সব রোগের তথ্য ও রোগীরা কী ওষুধ খাচ্ছেন তা চিকিৎসকদের জানা সম্ভব হয় না। তাই, অনেক সময় চিকিৎসকদের সঠিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রেসক্রিপশনে ভুলের পরিমাণ বেড়ে যায়।
হাতে লেখা প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম উদ্ধার করা রোগী ও ওষুধ বিক্রেতার নিকট অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই ওষুধ বিক্রেতারা অনেক সময় ধারণার উপরে ওষুধ দিয়ে দেন যার পরিণতি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।
ফার্মাসিস্ট থাকলে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে?
আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব নাজুক। হাসপাতালগুলোয় রোগীর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি রোগী ভর্তি হয়। তাই, চিকিৎসকদের সঠিক চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হয়। একটি সঠিক প্রেসক্রিপশন লিখতে যে সময় দেওয়া প্রয়োজন তা ডাক্তারদের থাকে না। রোগীর সব তথ্য নেওয়ার সময় থাকে না। এর ফলে প্রেসক্রিপশনে ভুল ডোজ ও ভুল ওষুধ লেখার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৭ জুলাই ২০২৪ কালের কণ্ঠের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, রোগী দেখার জন্য তিন মিনিটের বেশি সময় দিতে পারেন না চিকিৎসকরা। ফলে, প্রেসক্রিপশনে অনেক ভুল থেকে যায়। অন্যদিকে, ওষুধের দোকানে, হাসপাতালে এবং ক্লিনিকে ফার্মাসিস্ট না থাকায় ভুল প্রেসক্রিপশন সংশোধনেরও কোনো উপায় থাকে না।
উন্নত বিশ্বে চিকিৎসকরা একজন রোগীর পিছনে গড়ে ১০-২০ মিনিট সময় দেন, তারপরেও প্রেসক্রিপশনে অনেক ভুল থেকে যায়, যা ফার্মাসিস্টরা চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করে সংশোধন করে দেন। এ নিয়ে ডাক্তার-ফার্মাসিস্ট কোন দ্বন্দ্ব বাঁধে না। রোগীর নিরাপত্তাই সেখানে মুখ্য।
ওষুধ যেমন রোগ সারায়, ভুল ব্যবহার ও প্রয়োগে তা রোগও বাধায়, রোগীর অঙ্গহানি ঘটে এবং অনেক সময় রোগীর মৃত্যুও ঘটে। হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভিড় করা রোগীদের একটি বড় অংশ ওষুধের ভুল ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন সমস্যার স্বীকার বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশের ক্লিনিক-হাসপাতালগুলোয় রোগীর সংখ্যা ও রোগী মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব যদি ফার্মাসিস্টদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ওষুধ সম্পর্কিত ভুলগুলো কমিয়ে আনা যায়।
ড. মো. আজিজুর রহমান : অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আপনার মতামত দিন:
(মন্তব্য পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত। এর জন্য সম্পাদক দায়ী নন।)